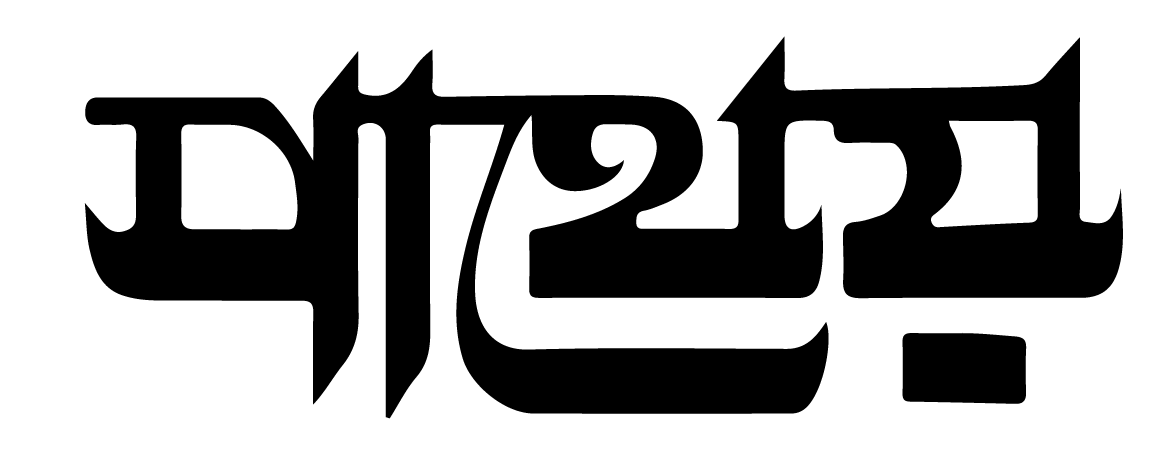পাথেয় টোয়েন্টিফোর ডটকম : একসময় শুধু দু-তিন বেলা খাবারের বিনিময়ে অন্যের জমিতে কাজ করতেন কৃষি শ্রমিকরা। পরে যুক্ত হয় নামমাত্র মজুরি। সেই মজুরিই বর্তমান বোরো মৌসুমে এলাকাভেদে ৪০০ থেকে সর্বোচ্চ এক হাজার ২০০ টাকা। তবু অনেক এলাকায় কৃষি শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না।
কৃষি শ্রমিকের সবচেয়ে বেশি মজুরি চট্টগ্রাম ও হাওরাঞ্চলের দুর্গম এলাকাগুলোয়। দৈনিক এক হাজার ২০০ টাকা। চাহিদাভেদে বাড়তি দুই বেলা খাবারও দিতে হয় কোথাও কোথাও। শ্রমিক খাটানো কৃষকের পাশাপাশি কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন, সংকটের কারণে অন্য এলাকা থেকে শ্রমিক আনতে হয়। তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা লাগে। আবার দুর্গম এলাকা হওয়ায় হারভেস্টার মেশিন ব্যবহার করা যায় না। এ কারণে শ্রমিকনির্ভর হতে হয় কৃষকদের।
মজুরিপ্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, এই বছর চুয়াডাঙ্গায় কৃষি শ্রমিকের মজুরি সবচেয়ে কম। দৈনিক ৪০০ টাকা। এর কারণ হিসেবে কৃষক ও কৃষি কমকর্তারা বলছেন, এই জেলায় বোরোর পাশাপাশি ভুট্টা চাষও হয় ব্যাপক হারে। ভুট্টা কাটা শেষ হয়ে যাওয়ায় জেলায় শ্রমিক সংকট নেই। এ কারণে এখানে শ্রমিকদের দর-কষাকষির সুযোগ কিছুটা কম।
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ব্যবসা ও বিপণন বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, গত ১০ বছরে কৃষি মজুরি প্রায় আট গুণ বেড়েছে। মজুরি বাড়ার কারণও যৌক্তিক। অকৃষি খাতে শ্রমিকরা বেশি মজুরি পাচ্ছেন। এ কারণেই কৃষিকাজে তাঁরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। শ্রমিক সংকটের আরেকটি বড় কারণ গ্রামীণ শ্রমিকদের শহরে বিভিন্ন বড় প্রকল্পের কাজে যুক্ত হওয়া। এসব কাজে দীর্ঘ মেয়াদে শ্রম বিক্রি করা যায়। আবার গ্রামে শিক্ষার ছোঁয়া লাগার কারণেও অনেকে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে মাটি-পানির কাজে আগ্রহ পাচ্ছেন না।
বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক হাসনীন জাহান জানান, ১৯৯১ সালে দেশে মোট শ্রমিকের প্রায় ৭০ শতাংশ ছিল কৃষি শ্রমিক। এর মধ্যে পুরুষ ছিল ৯১ শতাংশ এবং নারী মাত্র ৯ শতাংশ। আর ২০১০ সালে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪৮ শতাংশ; যার মধ্যে পুরুষ ৮৫ শতাংশ এবং নারী ১৫ শতাংশ। সর্বশেষ ২০২০ সালের প্রতিবেদনে কৃষি শ্রমিকের হার মোট শ্রমিকের ৩৮ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষ ৭৯ শতাংশ এবং নারী ২১ শতাংশ।
অর্থাৎ গত ৩০ বছরের কৃষি শ্রমিকের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রায় ৫০ শতাংশ কৃষি শ্রমিক কমেছে। তবে গত ৩০ বছরে কৃষিতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট তথ্য সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরোর কাছে পাওয়া যায়নি।
হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলা সদরের দত্তপাড়া গ্রামের কৃষক টুকুন কুমার দেব বলেন, ‘গত বছর যে জমি (ফসল) দেড় হাজার থেকে দুই হাজার টাকায় কাটিয়েছি, এবার সেই জমি আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার টাকায় কাটাতে হচ্ছে। আবার দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে এক হাজার থেকে এক হাজার ২০০ টাকা দিতে হচ্ছে।’
জাতুকর্ণপাড়া গ্রামের কৃষক ফজল মিয়া জানান, গভীর হাওরের (দূরবর্তী স্থান) তিন কেদার (৩০ শতাংশে এক কেদার) জমি কাটাতে ১৫ মণ ধান দিয়ে ১০ জন শ্রমিকের সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছেন। এতে খরচ বেড়ে গেছে।
ধান কাটা শ্রমিকদের ব্যাপারে বানিয়াচং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. এনামুল হক বলেন, যেসব গভীর হাওরের যোগাযোগব্যবস্থা খারাপ, অর্থাৎ যেখানে ধান কাটার মেশিন নেওয়া সম্ভব নয়; সেখানে শ্রমিকের ওপর নির্ভর করতে হয়।
সুনামগঞ্জের হাওরে কৃষি শ্রমিকরা টাকার চেয়ে ধানের বিনিময়ে ধান কাটেন বেশি। দৈনিক গড়ে একজন শ্রমিক প্রায় এক মণ ধান পান। এক একর জমি চাষ করতে কৃষকের প্রায় ১৫ হাজার টাকা খরচ হয়। ধান পান ৬০ থেকে ৭০ মণ।
কিশোরগঞ্জের হাওরাঞ্চলে কৃষি শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ৮০০ থেকে এক হাজার টাকা। ভরা মৌসুমে শ্রমিক সংকট দেখা দিলে আরো বেড়ে যায়। সেখানে এক একর বোরো জমিতে চাষাবাদ করতে খরচ হয় ৫০ থেকে ৫৫ হাজার টাকা। প্রতি একরে গড়ে ৭০ মণ ধান উৎপাদন হয়। ফসল কাটা-মাড়াই মৌসুমে ধানের দাম থাকে ৮০০ থেকে ৮৫০ টাকা। সে হিসাবে কৃষকরা এক একর জমিতে উৎপাদিত আধাপাকা ধান বিক্রি করে পান ৬০ থেকে ৬৫ হাজার টাকা।
জামালপুর সদরের পুগলই গ্রামের কৃষক মো. ইয়ানুছ আলীর ক্ষেতের বোরো ধান কাটছিলেন শ্রমিক ফয়জুল ইসলাম (৪০)। তিনি এসেছেন মাদারগঞ্জ উপজেলার বাজিতেরপাড়া থেকে। তিনি এসএসসি পাস। স্ত্রী ও তিন শিশুসন্তান নিয়ে তাঁর সংসার। তিনি বলেন, ‘এখন তো সার্বিক অবস্থা খুবই খারাপ। এই দুর্মূল্যের বাজারে সংসার চলে না। এখানে ৮০০ টাকা মজুরিতে ধান কাটতাছি। এই টাকা দিয়া কী অবো? মাছ, তেল আর আলু কিনতেই চলে যাবে।’
মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার কৃষি শ্রমিক রজব আলী বলেন, ‘জিনিসপত্রের দাম বেশি। ভালো মজুরি না পেলে কাজ করে পোষায় না। এখনকার সময়ে ৭০০ টাকা কিছুই না।’